প্রধান সব দলের অংশগ্রহণই মূল শর্ত
হাসান মামুন
প্রকাশ: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
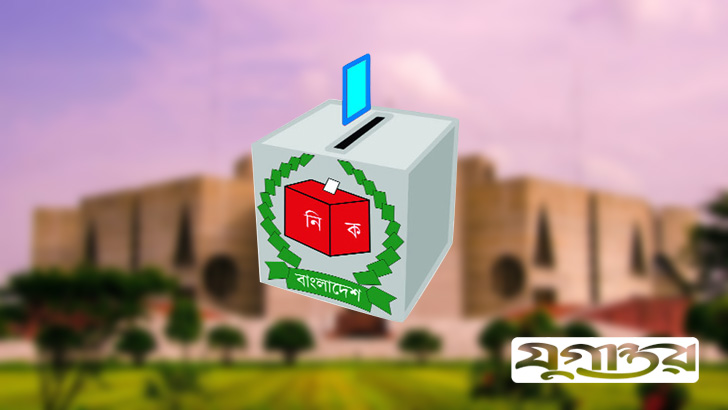
|
ফলো করুন |
|
|---|---|
শুধু জনগণের (অর্থাৎ ভোটার) একাংশ ভোট দিতে এলেই যদি নির্বাচন ‘অংশগ্রহণমূলক’ হতো, তাহলে সাম্প্রতিককালে যেসব জাতীয় ও উপনির্বাচন মোটেও গ্রহণযোগ্য হয়নি, সেগুলোকেও অংশগ্রহণমূলক বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। কারণ, এসব নির্বাচনেও কিছু না কিছু মানুষ ভোট দিতে এসেছিলেন। আর দেশে তো এমন কোনো বিধান নেই যে, ন্যূনতম কত শতাংশ ভোট পড়লে তবেই নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্য হবে। সাম্প্রতিককালের বেশকিছু নির্বাচনে এত কম ভোট পড়েছে যে, তাতে অনেকে বলতে শুরু করেছেন-এদেশেও ন্যূনতম ভোটের বিধান হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তো ভোট দিতে কখনো পিছিয়ে থাকেনি। নির্বাচনে সব বড় রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলে, নির্বাচনের একটা পরিবেশ থাকলে প্রবীণ আর পর্দানশীন মেয়েরাও উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসেন। গাঁটের পয়সা খরচ করে দূর থেকেও অনেকে ভোটকেন্দ্রে এসে হাজির হন। তার ভোটটি যেন অন্য কেউ দিয়ে দিতে না পারে, সেজন্য অনেকে কষ্ট করে হলেও সকাল সকাল চলে আসেন ভোটকেন্দ্রে। এদেশে ভোটের হার বাড়তে বাড়তে ৮৭ শতাংশ হয়ে যাওয়ার রেকর্ডও আছে। অথচ সাম্প্রতিককালে এমনও হয়েছে, সুনসান কেন্দ্রে ভোট দিতে আসার জন্য করতে হয়েছে মাইকিং।
এ অবস্থায় কেউ যদি বলে বসেন, আমরা তো ভোটারদের ধরে এনে ভোট দেওয়াতে পারি না, তারা ভোটকেন্দ্রে এলে আসবেন, না এলে নেই; সেক্ষেত্রে এ প্রশ্নটাই তুলতে হবে যে, ভোটাধিকার প্রয়োগে এ বিপুল অনাগ্রহের জায়গাটা কেন তৈরি হলো? বেশকিছু নির্বাচনে এত কম ভোট পড়েছে যে, তখন এ প্রশ্নও উঠেছে-‘আপনাদের বাঁধা ভোটাররাও কেন ভোট দিতে এলেন না?’ এর তৈরি জবাব অবশ্য রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ‘নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীর জয় নিশ্চিত জেনেই সমর্থকরা আর কষ্ট করে ভোট দিতে আসেননি।’ তখন সরলভাবে এ গরল প্রশ্নটা তুলতে হয় যে, আপনাদের প্রার্থীর জয় নিশ্চিত হলো কীভাবে? এর জবাবে আবার বলা হয়ে থাকে, ‘বিরোধী দল অংশ না নিলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো প্রার্থী না থাকলে তো এমনই হবে!’
তাহলে এ-ই দাঁড়াচ্ছে যে, নির্বাচনে ভোটারের স্বাভাবিক অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হলো প্রধান সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ। শুধু গোটাকতক সমমনা দল নির্বাচনে অংশ নিলেই ভোটাররা আগ্রহী হবেন না; বড় জনসমর্থন রয়েছে, এমন সব দলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। আর তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’। অনেক সময় দেখা যায়, বড় একটি দল নির্বাচনে অংশ নিতে এগিয়ে এলেও তাদের মনে হচ্ছে-লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত যে নির্বাচনগুলোকে আমরা গ্রহণযোগ্য বলে থাকি, তারও কোনো কোনোটিতে বিশেষ বিশেষ দলের কিন্তু মনে হয়েছিল-সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এমনটা মনে হয়েছিল। তারা এমনকি তখন নিজেদের মনোনীত রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ‘নির্লিপ্ততা’ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এরপর ওয়ান-ইলেভেন সরকার তার শাসনামলের দু’বছরের মাথায় যে নির্বাচন আয়োজন করে, তার ‘নিরপেক্ষতা’ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিএনপি। সেনাসমর্থিত ওই সরকারের চাপটা স্বভাবতই বেশি গিয়েছিল সদ্য রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে আসা বিএনপির ওপর দিয়ে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একটি দল হিসাবে অভিযোগ করতে করতেই তারা নির্বাচনে যায়; পরাজিতও হয় খারাপভাবে।
তাহলে দেখা যাচ্ছে, দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে কথা আছে। অবশ্য এর জবাবে বলা হয়ে থাকে, দলীয় সরকারগুলো পরবর্তী নির্বাচনে সুবিধা পাওয়ার জন্য বিশেষত জনপ্রশাসনকে এমনভাবে সাজিয়ে রেখে যায় যে, সেখানে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় একটা পরিবর্তন আনতেই হয়। ওয়ান-ইলেভেন সরকারকে তো নির্বাচন কমিশনও পুনর্গঠন করতে হয়েছিল। ভুয়া ভোটার বাদ দিয়ে প্রণয়ন করতে হয় নতুন তালিকা। তখনই আমরা প্রথম পাই ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা। তো, এসব জোরালো জবাব রয়েছে বলেই কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেও ‘বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার’ দলটি নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে। তাতে পরাজিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানালেও পরে ঠিকই অংশ নেয় জাতীয় সংসদে। কারণ, সেক্ষেত্রে নির্বাচনটি মোটা দাগে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তার সমর্থকগোষ্ঠীর কাছেও। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২০০১-এর নির্বাচনে অনেক কম আসন পেয়ে হেরে গেলেও আওয়ামী লীগ ভোট পেয়েছিল ৪০ শতাংশ। নির্বাচন ঠিকমতো না হলে এ বিপুলসংখ্যক ভোটার তাদের ভোট দিলেন কীভাবে?
এখন কথা হলো, নানা অভিযোগ তুলে ২০০১-এর নির্বাচনটি আওয়ামী লীগ বর্জনের পরও যদি বিএনপি নির্বাচনে থাকত এবং সংবিধান মানতে গিয়ে ওটা সেরেও ফেলতে হতো, তাহলে কি একই হারে মানুষ ভোট দিতে যেত ওই নির্বাচনে? কিংবা ২০০৮-এর নির্বাচনে বিএনপি যদি ওই সময়কার সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ‘আচরণে’ হতাশ হয়ে সেটা বর্জন করত, তাহলেও কি ৮৭ শতাংশ ভোটার গিয়ে হাজির হতো ভোটকেন্দ্রে? এদেশের বিপুল জনসমর্থনধন্য দুটি দল হলো বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। এরশাদ পতনের পর নতুন করে গণতন্ত্রের যে চর্চা শুরু হয়, তাতে এ দুটি দলই পালাক্রমে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। তবে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারব্যবস্থা উঠে যাওয়ার পর একেবারেই পালটে গেছে পরিস্থিতি। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন এদেশে যেমন হওয়ার কথা, তেমনই হচ্ছে এবং এতে ক্ষমতাসীন দলই জয়ী হয়ে সরকার গঠন করছে বারবার। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি একবার নির্বাচন বর্জন করেছে; আরেকবার অংশ নিলেও ‘প্রতারিত’ হয়েছে বলে অভিযোগ করছে। দ্বিতীয় নির্বাচনে আগের রাতেই সিংহভাগ কেন্দ্রে ‘ভোট’ সম্পন্ন করে ফেলা হয় বলে অভিযোগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েও ছড়িয়েছে।
এ অবস্থাতেই সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, সামনের নির্বাচনটি ২০১৪ বা ২০১৮-এর মতো হবে না। এদেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা অনুযায়ী সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে। জবাবে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আমরা তো এমন আশ্বাসে আস্থা রেখে ২০১৮-এর নির্বাচনে গিয়েছিলাম। তাতে অভিজ্ঞতা মোটেও ভালো হয়নি। এর আগে ২০১৪-এর নির্বাচনে ১৫৩ আসনে নজিরবিহীনভাবে কোনো ভোটই হয়নি। বিএনপি বারবারই মনে করিয়ে দিচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন-সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য নির্বাচনটা ওভাবে করতে হলেও অচিরেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়া হবে। সেটা আর হয়নি। অব্যাহত মামলা-হামলা দিয়ে মাঠের বিরোধী দলকে বরং আরও কোণঠাসা করা হয়েছে বলেই তাদের অভিযোগ। দীর্ঘদিন তাদের নির্বাচন ও ক্ষমতার বাইরে রেখে প্রান্তিক করে ফেলাই সরকারের লক্ষ্য বলে বিএনপির বক্তব্য ক্রমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। দেশে-বিদেশে এটি পেয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতাও।
এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি নির্বাচনে না এলেও ভোটারের একটা ক্ষুদ্রাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেই নির্বাচন ‘অংশগ্রহণমূলক’ হবে বলে যারা মনে করছেন, তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ বলেই মনে হয়। কিংবা সঠিক উপলব্ধিতে পৌঁছতে তাদের বিশেষ সমস্যা রয়েছে। যা হোক, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মূল শর্ত হলো প্রধান সব দলের অবাধ অংশগ্রহণ। এটি নিশ্চিত হলে সেসব দলের সমর্থক তো বটেই, এমনকি যারা একেক সময় একেক দলের প্রার্থীকে জেতাতে চান, তারাও উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসবেন ভোট দিতে। এর আগে তারা নির্বাচনি প্রচারেও শামিল হবেন, খোঁজখবর রাখবেন, ঘরে-বাইরে অংশ নেবেন রাজনৈতিক আলাপে। এ ধরনের একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে তৃণমূল পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারিভাবে অনেক অর্থ খরচ হবে আর তাতে চাঙা হয়ে উঠবে অর্থনীতি। কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত আগের ধারাতেই নির্বাচন হয়, তাহলে দেখা যাবে ক্ষমতাসীন দল ও তার মিত্রদের ভোটাররাও অত উৎসাহবোধ করছেন না নির্বাচনে। হয়তো দেখা যাবে, ১০-১৫ শতাংশ ভোট আর সঙ্গে কিছু একতরফা জাল ভোটে পার হয়ে গেল নির্বাচনের দিনটি। এর ফল কী হবে, তা তো আগে থেকেই জানা।
এমন নির্বাচন আয়োজন করে দেশের এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় না করাই ভালো। সেক্ষেত্রে হয়তো সংবিধানের দোহাই দেওয়া হবে। ‘সংবিধান অনুযায়ী’ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কেমন হয়, তা কি আমরা দেখিনি? একই জিনিস নতুন করে দেখতে হবে কেন? এদেশে অতীতেও কিন্তু সুষ্ঠু, অবাধ ও ‘অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন’ হতো না। অভিজ্ঞতার নিরিখে তার ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোই করেছিল। সেটি খুব বেশিদিন আগের কথাও নয় যে, মানুষ ভুলে যাবে। জনমনে এ স্মৃতি বরং তরতাজা যে, দলীয় সরকারের অধীনে দু-দুটি নির্বাচন কেমন হয়েছে। দেশের সিংহভাগ মানুষ এ ধরনের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি চায় কিনা, সেটি জানতে কি গণভোটের আয়োজন করতে হবে? সব দল-মতের মানুষ যাতে একটা অংশগ্রহণমূলক ও অর্থবহ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের সুযোগ পায়, সেটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। খালি নিজ সুবিধামতো কথাবার্তা বলে এ দাবি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হতে থাকলে তা কারও জন্যই সুফল বয়ে আনবে না।
হাসান মামুন : সাংবাদিক, বিশ্লেষক
